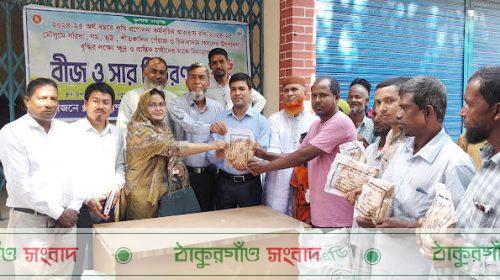লেখক অধ্যাপক মোঃ করিমুল হক
ভৌগোলিক পরিচিতিঃ
বাংলাদেশের উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁও। আর ঠাকুরগাঁও জেলার সর্ব দক্ষিণে ভারতের সীমান্ত ঘেঁসে অবস্থান হরিপুর উপজেলার। ১৯১০ সালে রাণীশংকৈল থানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গঠিত হয় হরিপুর থানা এবং ১৯৮৩ সালে আপগ্রেড থানা হিসাবে তা উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত হরিপুর উপজেলা দিনাজপুর জেলার অধীনস্থ ছিল। ঐ বছরের ১ ফেব্রুয়ারী ঠাকুরগাঁও মহকুমা কে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হলে হরিপুর উপজেলা ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। হরিপুর উপজেলার আয়তন ২০১.০৬ বর্গকিলোমিটার এবং বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১,৫৫,৭৯৮ জন। পূর্ব-দক্ষিণে কুলিক এবং পশ্চিমে নাগর নদী বেষ্টিত হরিপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলিম। হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত অধিবাসী ১২ শতাংশের কাছাকাছি। ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তাবা নৃ-গোষ্ঠী সামান্যই, যার মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত মাঝারী। প্রাচীন হরিপুর আরণ্যক আর অনুর্বর হলেও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির কারণে হালের হরিপুর উর্বর এবং সবুজের সমারোহে ভরপুর। এখানকার মাটি বেলে এবং বেলে-দোঁয়াশ। প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান, পাট, ভুট্টা, গম এবং সরিষা। প্রাকৃতিক খাল-বিল এবং খননকৃত অসংখ্য দীঘি-পুকুরে মাছচাষ, আর উর্বর বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে লক্ষ্য করা যায় আধুনিক আমের বাগান। শিক্ষার হার ৪২.১০, যা বর্তমানে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার প্রায় ৯০ ভাগ কৃষিজীবি। বাকি ১০ শতাংশের মধ্যে আছেন বিচারপতি, সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষক, ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার এবং ব্যাংকার সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ।
জেলা সদর থেকে এই উপজেলার দূরত্ব ৬২ কিলোমিটার। উত্তর ও পশ্চিম দিকে রাণীশংকৈল উপজেলা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে ভারতের উত্তর দিনাজপুর জেলা বেস্টিত হরিপুর উপজেলা মূলতঃ ইংরেজি অক্ষর “এল” আকৃতির। সর্ব উত্তরে গেদুড়া ইউনিয়ন, এরপর ক্রমশঃ দক্ষিণে আমগাঁও, বকুয়া, ডাঙ্গীপাড়া, হরিপুর সদর এবং পূর্বে ভাতুরিয়া ইউনিয়ন। ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ ভাগের পর থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত হরিপুরে গেদুড়া, বীরগড় এবং জীবনপুর নামে ৩টি ইউনিয়ন ছিল। ইউনিয়ন গুলোকে “ইউনিয়ন বোর্ড” এবং এর প্রধান কে বলা হতো “বোর্ড প্রেসিডেন্ট “। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান ইউনিয়ন বোর্ড কে ” ইউনিয়ন কাউন্সিল” এবং বোর্ড প্রেসিডেন্টকে “ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান ” নামে অভিহিত করে এক সামরিক ফরমান জারি পূর্বক তা বাস্তবায়ন করেন।
১৯৭৩ সালের শেষদিকে বাংলাদেশ সরকার প্রাগুক্ত ৩টি ইউনিয়নকে ৬টি ইউনিয়নে বিভক্ত করে ইউনিয়ন কাউন্সিল গুলোকে “ইউনিয়ন পরিষদ” নামে গেজেট ভুক্ত করেন। এ সময় গেদুড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল ভেঙ্গে ১নং গেদুড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও ২নং আমগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, বীরগড় ইউনিয়ন ভেঙ্গে, ৩নং বকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪নং ডাঙ্গীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, এবং জীবনপুর ইউনিয়ন ভেঙ্গে, ৫নং হরিপুর ও ৬নং ভাতুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর, ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে নবগঠিত ইউনিয়ন পরিষদ গুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে গেদুড়া ইউনিয়নে মোঃ এলাহী বকস, আমগাঁও ইউনিয়নে ডাক্তার মোঃ সফির হোসেন, বকুয়া ইউনিয়নে মোঃ কমরউদ্দীন, ডাঙ্গীপাড়া ইউনিয়নে হামিদুর রহমান চৌধুরী, হরিপুর ইউনিয়নে মোঃ আবদুল্লাহ এবং ভাতুরিয়া ইউনিয়নে মোঃ বাহাদুর হোসেন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
হরিপুরের জমিদার ও ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ীঃ
হরিপুর ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্র এবং উপজেলা সদরের নতুন বাজার সংলগ্ন কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঐতিহাসিক হরিপুর জমিদার বাড়ী, যা স্থানীয় ভাবে হরিপুর “রাজবাড়ী” নামে অধিক পরিচিত।
দিল্লীর সম্রাট মহামতি আকবরের শাসনামলে ভূ-রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সংস্কার কালে সর্বপ্রথম জমিদারী প্রথার উন্মেষ ঘটে। জমির খাজনা আদায়ের জন্য সমগ্র দেশকে বিভক্ত করা হয় সুবা(প্রদেশ), সরকার এবং পরগনায়।একাধিক পরগণা নিয়ে গঠিত হয় “সরকার”। হরিপুর জমিদারদের সরকার ছিল বর্তমান ভারতের উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ থানায় অবস্থিত “সরকার তাজপুর”। পরগণা গুলোর জমির মালিকানা দেওয়া হয় জমিদারদের। আর জমিদাররা থাকতো সরকারের অধীন। জমিদারগণ পরগনার অন্তর্ভুক্ত জমির বাৎসরিক খাজনা আদায় করে সরকারের রাজকোষে জমা দিতেন। সম্রাট কর্তৃক মনোনীত ফৌজদার বা শিকদার থাকতেন সরকারের প্রশাসন ও রাজকোষের দায়িত্বে। উল্লেখ্য যে, মোঘল আমলে বেশিরভাগ জমিদার ছিলেন মুসলমান। আর জমিদারের অধিকাংশ রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ভূক্ত ব্যক্তিবর্গ। ফলে সরকারের সঙ্গে রাজস্ব কর্মচারীদের লেনদেনের মাধ্যমে বিশেষ যোগাযোগ ও সখ্যতা গড়ে উঠে।
১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্বের জমিদারী প্রথা বাতিল করে বৃটিশ ধাচের জমিদারী ব্যবস্থা চালু করলে মুসলমান জমিদারদের কপাল পুড়ে এবং নিম্নবর্গের রাজস্ব কর্মচারীরা রাতারাতি নতুন জমিদার বনে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার জমিদারগণকে জমির এককালীন মালিকানা প্রদান করে স্থায়ীত্ব দেন। যা ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পূর্ব পর্যন্ত বলবত ছিল।যতদূর জানা যায়, খোলড়া এবং ভাতুরিয়া পরগণা ছিল হরিপুর জমিদারীর অধীন। ফলে হরিপুর জমিদার কর্তৃক আদায়কৃত খাজনা জমা দিতে হতো “সরকার তাজপুরের” খাজাঞ্চি খানার ফৌজদার বা শিকদারের কাছে।
(পরবর্তী অংশ আসছে……)
তথ্য সূত্রঃ
১। অংগীকার, করিমুল হক মনজু সম্পাদিত, ১৯৮৬ খ্রিঃ।
২। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, মোঃ মকসেদুর রহমান, ১৯৮৮ খ্রিঃ।
৩। উপাজেলা পরিসংখ্যান অফিস, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।
৪। আইন-ই-আকবরী, ডঃ আবুল ফজল।